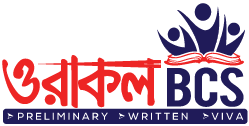প্রকৃতি ও প্রত্যয়
প্রকৃতি
ক্রিয়া বা শব্দের মূলই প্রকৃতি। কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনোভাবেই বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না,
তাকে প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ যে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাই প্রকৃতি। ক্রিয়াপদের মূল অংশকেও প্রকৃতি বলে।
প্রাতিপদিক: বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন- মিঠা + আই = মিঠাই, মধু + র = মধুর। এখানে ‘মিঠা’ ও ‘মধু’ প্রাতিপদিক।
প্রকৃতি দুই প্রকার। যথা:
ক্স ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি: ক্রিয়ার মূল অংশকে বলা হয় ধাতু। ধাতু কথাটি বোঝানোর জন্য ধাতুর আগে (√) চিহ্নটি ব্যবহার করতে হয়।
এই চিহ্ন ব্যবহার করলে ‘ধাতু’ কথাটি লেখার প্রয়োজন হয় না।
যেমন- √র্ক (র্ক ধাতু), √পড় (পড় ধাতু) ইত্যাদি। প্রকৃতি ও প্রত্যয়
ক্স নাম প্রকৃতি বা প্রাতিপদিক: নামপদের মূল অংশকে বলে নাম প্রকৃতি। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে।
যেমন: মা, গাছ, শির, লতা, মুখ, পা, বই ইত্যাদি।
প্রত্যয়
যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং প্রাতিপদিক বা নাম শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।
প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা: ক. কৃৎ-প্রত্যয় ও খ. তদ্ধিত প্রত্যয়।
কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। প্রকৃতি ও প্রত্যয়
তৎসম বা সংস্কৃত প্রকৃতির সঙ্গেও অনুরূপভাবে কৃৎ-প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত পদ সাধিত হয়।
যেমন √গম্+অন=গমন, √কৃ+তব্য=কর্তব্য
কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করলে কৃৎ-প্রকৃতির আদিস্বর পরিবর্তিত হয়।
এ পরিবর্তনকে বলা হয় গুণ ও বৃদ্ধি।
গুণ: (ক) ই, ঈ-স্থলে এ, (খ) উ, ঊ-স্থলে ও এবং (গ) ঋ-স্থলে র্অ হয়।
যেমন √চিন্+আ=চেনা (ই স্থলে এ হলো); (নী+আ=নেওয়া (ঈ স্থলে এ); √ধু+আ = ধোয়া (উ স্থলে ও) ; কৃ+তা = করতা কর্তা (ঋ স্থলে র্অ)।
বৃদ্ধি: (ক) অ-স্থলে আ, (খ) ই ও ঈ-স্থলে ঐ, (গ) উ ও ঊ স্থলে ঔ এবং (ঘ) ঋ-স্থলে র্আ হয়। যেমন
প”্ + অ (ণক) পাচক (পচ-এর অ স্থলে ‘আ’); শিশু+ অ(ষ্ণ) = শৈশব (ই স্থলে ঐ); যুব + অন= যৌবন (উ স্থলে ঔ); কৃ+ঘ্যণ= কার্য (ঋ স্থলে র্আ)।